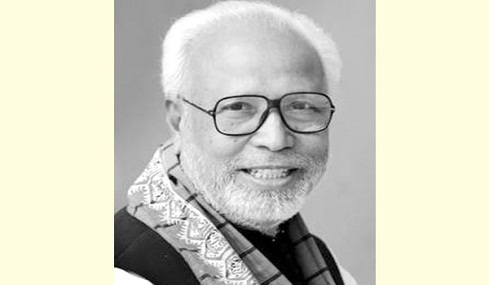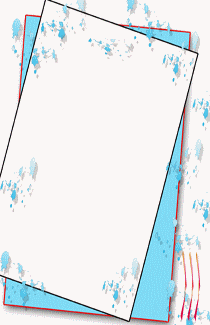বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম : যেখানে পাকিস্তানি হানাদারদের গুলিতে ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট আমার মরার কথা, সেখানে মাত্র চার বছর পর ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ আমার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা, আমার হৃদস্পন্দন, চোখের আলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে ধানমন্ডির ৩২-এ নির্মমভাবে নিহত হন। আল্লাহর কি অপার কুদরত, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমার চলে যাওয়ার কথা সেখানে বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। কেন যে আমাকে নিলেন না, কী অপরাধ ছিল, কোথায় আমার ব্যর্থতা কত খুঁজলাম এখনো তার নাগাল পেলাম না। ’৭৫-এর পর আগস্ট এলেই ভালো লাগে না। কেমন একটা খেইহারা হয়ে যাই। ’৬৫-এর শুরুতে বাড়ি থেকে পালিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে গিয়েছিলাম। স্থান হয়েছিল ১ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে। যুদ্ধ শেষে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হলো। স্থান হলো চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসার পাশে পাহাড়ের কোলে ৬ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন কেবলই রেজিমেন্ট তৈরি হচ্ছিল। কিছুদিন পর নিয়ে আসা হলো ময়নামতি পাঞ্জাব লাইনে। একসময় নানা তদবির করে নানা ঝকমারি মোকাবিলা করে বাড়ি ফিরলাম লেখাপড়া করতে। পরের বছর ম্যাট্রিক দেব। বড় ভাই জেলখানা থেকে লিখলেন, ‘এবারই পরীক্ষা দেও। সেনাবাহিনীতে গিয়ে তুমি তো মূর্খ হওনি। কিছুটা লেখাপড়া করেছ। আর বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।’ পরীক্ষার তিন মাস বাকি। যে মানুষ পড়তেই বসতাম না, সেই মানুষ রাতদিন পড়ালেখা শুরু করলাম। অনেক রাতে অনেকবার মা বই নিয়ে গিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম। গেলাম করটিয়া সাদৎ কলেজে। সেখানে নানা ঝকমারি করে ভর্তি হলাম। বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী তখন জেলে। আমি হাত পায়ে তালপাত সিং লতিফ সিদ্দিকীর ভাই বলে আমার কাছে অনেকের অনেক আশা। কিন্তু আমি যে নিরেট গর্দভ একেবারে অপদার্থ এর জন্য খেসারত দিতে হলো অনেক। ছাত্রলীগ করি। নাক ঢেকে স্লোগান দিই, মিছিল করি। কিন্তু সভা-সমাবেশের সময় পালিয়ে বেড়াই। বক্তৃতায় নাম ঘোষণা করে আমাকে পায় না। এভাবে চলে বেশ কিছুদিন। উপায় নেই তাই নদীর চরে গিয়ে হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করতাম। যা মনে হতো তা-ই বলতাম। এমনি করতে করতে একবার বাসাইল উপজেলার বর্ণী প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সামনে হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করেছিলাম। ফিরে আসার পথে মনে হলো আমি যা বলতে চেয়েছি তা বলতে পেরেছি। এরপর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সভা-সমাবেশে কথা বলা শুরু করলাম। চলে গেল আরও কিছুদিন। তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয়েছে। আন্দোলনও তীব্র হচ্ছে। এর মধ্যে ছাত্রদের ১১ দফা ছাত্রসমাজকে উদ্বেলিত করে তুলল। ছয়-সাত মাস আগে যে পরিমাণ লোকজন হতো তার ১০ গুণ হওয়া শুরু হয়ে গেল। ছাত্রদের মধ্যে তখন কোনো দলাদলি নেই, হলাহলি নেই- সবাই এক। এমনকি মোনায়েম খানের ছাত্র সংগঠন এনএসএফের বড় অংশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হলো। মূল রাজনৈতিক .jpg) দলগুলো তেমন তৎপর ছিল না। কিন্তু ছাত্র-যুবরা সব মরিয়া। আমরা ৫০ জন নিয়ে মিছিল শুরু করলে শেষ হতো ৫ হাজারে। মানুষ ছটফট করছিল। দিন দিন আন্দোলনের সমর্থন বাড়ছিল। এর মধ্যে ’৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে আসাদ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন। তখন মানুষের কাছে ছাত্রনেতা ছাত্রদের অপরিসীম গুরুত্ব। রাজা-বাদশাহদের সম্মানের চেয়ে বেশি। তোফায়েল আহমেদ মুকুটহীন সম্রাট। আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজের নাম আকাশে বাতাসে। আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি, কে এম ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে গেছেন। আসাদের হত্যার পর আইয়ুব খান আর বেশিদিন টেকেননি। ২১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিলে বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে ছাত্র আন্দোলনের মহানায়ক তোফায়েল আহমেদ ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এদিকে আমাদের গুরু রাজনৈতিক ঠিকানা লতিফ সিদ্দিকী ময়মনসিংহ জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। আমরা তো জেগেই ছিলাম। লতিফ সিদ্দিকীকে পেয়ে আরও উজ্জীবিত হলাম। কদিন পরই এলেন ইয়াহিয়া খান। আইয়ুব খানের বিদায়। ’৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জাকে বিতাড়িত করে আইয়ুব খান এসেছিলেন, ’৬৯ সালে আইয়ুব খানকে বিতাড়িত করে ইয়াহিয়া খান। মার্চ থেকে ডিসেম্বর রাজনীতি নিষিদ্ধ। তবে ঘরোয়া রাজনীতি চালু থাকল। রাজনৈতিক অফিস-আদালত খোলা, ’৭০-এর পয়লা জানুয়ারি রাজনীতি মুক্ত হলো, নির্বাচনী প্রস্তুতি নেওয়া হলো। তখন ঘরে ঘরে বঙ্গবন্ধু, ঘরে ঘরে নৌকা। ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর ’৭০-এ দেশে নির্বাচন হলো। ১৬৯ আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু পেলেন ১৬৭টি। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১টি। মানুষ ভাবল শান্তি আসবে সুস্থিতি আসবে। বুক বাধল তারা। ৩ জানুয়ারি নৌকার মঞ্চ বানিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু সব সদস্যকে শপথ পড়ালেন। সেই ভাষণ তিনি শেষ করেছিলেন ‘জয় বাংলা জয় পাকিস্তান’ বলে। সেটা শুনে অনেকেই বলেন, নেতার ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে ‘জয় বাংলা জয় পাকিস্তান’ বলে শেষ করেছিলেন। আদতে কখনো না। তিনি জয় পাকিস্তান বলেছিলেন ৩ জানুয়ারি আর ৭ মার্চের ভাষণ তো ৭ মার্চেই; মাঝে মাত্র এক মাস কয়েকদিন। পাকিস্তান জনগণের রায় মানেনি। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বললেন, ‘যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। আমরা যখন মরতে শিখেছি কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।’ ৭ মার্চের আগেই ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ভিপি আ স ম আবদুর রবের হাতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে শাজাহান সিরাজের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, রাষ্ট্রপতি এসব ঘোষণা করা হয়েছিল। বাকি ছিল না কোনো কিছুই। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ শেষ করেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ বলে। ২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া খান নানা রকমের আলোচনা চালিয়ে সময় নষ্ট করে সময়মতো বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃবৃন্দের যতটা অংশ থাকার কথা তা ছিল না। যে কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো দ্বিধা না থাকলেও অনেক নেতার মধ্যে ‘হারিয়ে’ যাওয়ার সন্দেহ ছিল। প্রায় সবাই জীবন বাঁচাতে চলে গিয়েছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ করেছিলেন। বলতে লজ্জা হয়, অনেক নেতা পালিয়েও গিয়েছিলেন। সে যা হোক, পালাতে দ্বিধা হচ্ছিল। একসময় হাত-পা ছুড়ে বক্তৃতা করেছি, ‘প্রয়োজনে দেশের জন্য জীবন দেব’। তাই যখন জীবন দেওয়ার সময় এলো তখন পালিয়ে গেলে মানুষ হতাশ হবে। তা ছাড়া নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে দেখে, বাড়িঘর জ্বালানোয়, মা-বোনের সম্মান-সম্ভ্রম নষ্ট করা দেখে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ১১ আগস্ট কাদেরিয়া বাহিনী হানাদার পাকিস্তানিদের দুটি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ দখল করে। ১২ ও ১৩ আগস্ট প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এমনকি বিমান হামলা হচ্ছিল বারবার। ২-৩টি পাকিস্তানি স্যাবরজেট চরের বালুমাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্ধকার করে ফেলেছিল। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় আমরা ভূঞাপুর ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছিলাম। এ যুদ্ধে পাকিস্তানিরা অনেক শক্তি প্রয়োগ করলেও আমাদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। মাত্র দু-তিন জন যোদ্ধা সামান্য আহত হয়েছিলেন। ভূঞাপুর থেকে কিছু পুবে গলগন্ডায় রাত কাটিয়েছিলাম। ১৪ তারিখ সেখানেও যুদ্ধ হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের ওপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেখানে কমান্ডার খোরশেদ আলম বীরপ্রতীক দারুণভাবে আহত হয়। সে খুব কান্নাকাটি করছিল, ‘স্যার আপনি আমার ধর্মের বাপ। আমাকে ফেলে যাবেন না।’ বলেছিলাম, আহতদের ফেলে গেলে যুদ্ধ চলবে কী করে! অন্যদের মনোবল ভেঙে যাবে। আমরা তোমাকে নিয়ে শেষ চেষ্টা করব। তাকে নিয়ে আমরা পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলাম। পোড়াবাড়ির বটতলীতে রাত কাটিয়েছিলাম। তারপর সন্ধানপুর। সেখান থেকে পেঁচার হাট। তারপর আহত খোরশেদকে বুলবুল খান মাহবুব ও নুরুন্নবীর সঙ্গে মহানন্দপুর কাদেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধকালীন হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর সেই খোরশেদ আলম সুস্থ হয়েছিল। ৯০-৯৫ বছর বয়সে আল্লাহ তাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন।
দলগুলো তেমন তৎপর ছিল না। কিন্তু ছাত্র-যুবরা সব মরিয়া। আমরা ৫০ জন নিয়ে মিছিল শুরু করলে শেষ হতো ৫ হাজারে। মানুষ ছটফট করছিল। দিন দিন আন্দোলনের সমর্থন বাড়ছিল। এর মধ্যে ’৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে আসাদ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন। তখন মানুষের কাছে ছাত্রনেতা ছাত্রদের অপরিসীম গুরুত্ব। রাজা-বাদশাহদের সম্মানের চেয়ে বেশি। তোফায়েল আহমেদ মুকুটহীন সম্রাট। আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজের নাম আকাশে বাতাসে। আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি, কে এম ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে গেছেন। আসাদের হত্যার পর আইয়ুব খান আর বেশিদিন টেকেননি। ২১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিলে বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে ছাত্র আন্দোলনের মহানায়ক তোফায়েল আহমেদ ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এদিকে আমাদের গুরু রাজনৈতিক ঠিকানা লতিফ সিদ্দিকী ময়মনসিংহ জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। আমরা তো জেগেই ছিলাম। লতিফ সিদ্দিকীকে পেয়ে আরও উজ্জীবিত হলাম। কদিন পরই এলেন ইয়াহিয়া খান। আইয়ুব খানের বিদায়। ’৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জাকে বিতাড়িত করে আইয়ুব খান এসেছিলেন, ’৬৯ সালে আইয়ুব খানকে বিতাড়িত করে ইয়াহিয়া খান। মার্চ থেকে ডিসেম্বর রাজনীতি নিষিদ্ধ। তবে ঘরোয়া রাজনীতি চালু থাকল। রাজনৈতিক অফিস-আদালত খোলা, ’৭০-এর পয়লা জানুয়ারি রাজনীতি মুক্ত হলো, নির্বাচনী প্রস্তুতি নেওয়া হলো। তখন ঘরে ঘরে বঙ্গবন্ধু, ঘরে ঘরে নৌকা। ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর ’৭০-এ দেশে নির্বাচন হলো। ১৬৯ আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু পেলেন ১৬৭টি। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১টি। মানুষ ভাবল শান্তি আসবে সুস্থিতি আসবে। বুক বাধল তারা। ৩ জানুয়ারি নৌকার মঞ্চ বানিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু সব সদস্যকে শপথ পড়ালেন। সেই ভাষণ তিনি শেষ করেছিলেন ‘জয় বাংলা জয় পাকিস্তান’ বলে। সেটা শুনে অনেকেই বলেন, নেতার ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে ‘জয় বাংলা জয় পাকিস্তান’ বলে শেষ করেছিলেন। আদতে কখনো না। তিনি জয় পাকিস্তান বলেছিলেন ৩ জানুয়ারি আর ৭ মার্চের ভাষণ তো ৭ মার্চেই; মাঝে মাত্র এক মাস কয়েকদিন। পাকিস্তান জনগণের রায় মানেনি। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বললেন, ‘যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। আমরা যখন মরতে শিখেছি কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।’ ৭ মার্চের আগেই ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ভিপি আ স ম আবদুর রবের হাতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে শাজাহান সিরাজের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, রাষ্ট্রপতি এসব ঘোষণা করা হয়েছিল। বাকি ছিল না কোনো কিছুই। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ শেষ করেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ বলে। ২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া খান নানা রকমের আলোচনা চালিয়ে সময় নষ্ট করে সময়মতো বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃবৃন্দের যতটা অংশ থাকার কথা তা ছিল না। যে কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো দ্বিধা না থাকলেও অনেক নেতার মধ্যে ‘হারিয়ে’ যাওয়ার সন্দেহ ছিল। প্রায় সবাই জীবন বাঁচাতে চলে গিয়েছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ করেছিলেন। বলতে লজ্জা হয়, অনেক নেতা পালিয়েও গিয়েছিলেন। সে যা হোক, পালাতে দ্বিধা হচ্ছিল। একসময় হাত-পা ছুড়ে বক্তৃতা করেছি, ‘প্রয়োজনে দেশের জন্য জীবন দেব’। তাই যখন জীবন দেওয়ার সময় এলো তখন পালিয়ে গেলে মানুষ হতাশ হবে। তা ছাড়া নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে দেখে, বাড়িঘর জ্বালানোয়, মা-বোনের সম্মান-সম্ভ্রম নষ্ট করা দেখে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ১১ আগস্ট কাদেরিয়া বাহিনী হানাদার পাকিস্তানিদের দুটি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ দখল করে। ১২ ও ১৩ আগস্ট প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এমনকি বিমান হামলা হচ্ছিল বারবার। ২-৩টি পাকিস্তানি স্যাবরজেট চরের বালুমাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্ধকার করে ফেলেছিল। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় আমরা ভূঞাপুর ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছিলাম। এ যুদ্ধে পাকিস্তানিরা অনেক শক্তি প্রয়োগ করলেও আমাদের তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। মাত্র দু-তিন জন যোদ্ধা সামান্য আহত হয়েছিলেন। ভূঞাপুর থেকে কিছু পুবে গলগন্ডায় রাত কাটিয়েছিলাম। ১৪ তারিখ সেখানেও যুদ্ধ হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের ওপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেখানে কমান্ডার খোরশেদ আলম বীরপ্রতীক দারুণভাবে আহত হয়। সে খুব কান্নাকাটি করছিল, ‘স্যার আপনি আমার ধর্মের বাপ। আমাকে ফেলে যাবেন না।’ বলেছিলাম, আহতদের ফেলে গেলে যুদ্ধ চলবে কী করে! অন্যদের মনোবল ভেঙে যাবে। আমরা তোমাকে নিয়ে শেষ চেষ্টা করব। তাকে নিয়ে আমরা পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলাম। পোড়াবাড়ির বটতলীতে রাত কাটিয়েছিলাম। তারপর সন্ধানপুর। সেখান থেকে পেঁচার হাট। তারপর আহত খোরশেদকে বুলবুল খান মাহবুব ও নুরুন্নবীর সঙ্গে মহানন্দপুর কাদেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধকালীন হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর সেই খোরশেদ আলম সুস্থ হয়েছিল। ৯০-৯৫ বছর বয়সে আল্লাহ তাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন।
১৯৭১-এর ১৬ আগস্ট মরে যাওয়ার কথা আমার। কিন্তু তার মাত্র চার বছর পর আমাদের এতিম করে চলে গেলেন জাতির পিতা। ১৫ আগস্ট সুবেহ সাদিকে পাকিস্তানের কয়েকজন পেতাত্মা তথাকথিত বিপথগামী সেনা সদস্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির গৌরব সেনাবাহিনী। পৃথিবীর সব সেনাবাহিনীর আমাদের মতো গর্ব করার কিছু নেই। দেশ হয় তারপর সেনাবাহিনী তৈরি হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী হয়েছে, তারপর দেশ। কত গর্বের কথা। বঙ্গবন্ধু নিহত হলে এক কাপড়ে ঘর ছেড়েছিলাম। ১৬ বছর আর ঘরে ফেরা হয়নি। এ সময় পলে পলে উপলব্ধি করেছি, বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে প্রকৃত সেনাবাহিনী কখনো জড়িত ছিল না। অথচ ষড়যন্ত্রকারীরা কৌশলে সেনাবাহিনীর বদনাম করেছে। অনেকের এখনো ধারণা, সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। মোটেই তা নয়। প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখেছি, কত বড় বড় সেনা অফিসার যোগাযোগ করেছেন, ‘যখন বলবেন তখনই আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়াব। বঙ্গবন্ধুর হত্যা আমরা চাইনি। এর দায় আমরা কোনোভাবেই নেব না।’ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সেদিন যারা জীবনের কথা চিন্তা না করে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হত্যার প্রতিবাদ করেছিল আজ আমার বোনের শাসনামলে তারাই বরং নিন্দিত, অবহেলিত। পিতার চামড়া দিয়ে যারা ডুগডুগি বাজাতে চাইত, ‘জাতির পিতা না জুতার ফিতা’ বলত তারা কত আরামে, কত দাপটে। কিন্তু ’৭৫-এর প্রতিরোধ যোদ্ধারা এখনো স্বীকৃতি পেল না। তারা সবাই দুষ্কৃতকারী। জিয়ার সময়, এরশাদের সময়, বেগম খালেদা জিয়ার সময় দুষ্কৃতকারী হিসেবে নিজেদের গর্ব হতো। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার আমলে বড় দুঃখ হয়, অবিচার বলে মনে হয়।
বঙ্গবন্ধু নিহত হলে যৌবনে সোনার দিনগুলো ভারতে কাটিয়েছি। নানা দিক থেকে আগস্ট আমার প্রিয় হতে পারত। কারণ ১৪ আগস্ট আমার স্ত্রীর জন্মদিন। কিন্তু ’৭৫-এর পর প্রতিটি আগস্ট আমাকে কাঁদায়, আমাকে ভাবায়, আমার ভিতরে কাঁপন তোলে। সেদিন এমনিতেই মনটা ভারী ছিল। সারা দুনিয়ার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, ‘আমরা বেহেশতে আছি।’ ভদ্রলোক কবে যে বেহেশত দেখে এলেন কিছুই জানি না। তবে রাস্তাঘাটে মানুষের যে অবস্থা, বাজারে যেমন আগুন তাতে সাধারণ লোকজন সামনে পেলে খুব একটা সমাদর করবে না। তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মানুষের মাথায় নয়, পেটে আগুন জ্বালিয়েছে। আমার বোন কেন যে ভাবলেশহীন বোধের অভাবী এসব লোককে অত উচ্চপদ দিয়ে দেশের ক্ষতি করছেন বুঝতে পারছি না। গিয়েছিলাম টাঙ্গাইলে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। গেটে পাহারাদাররা ঢুকতে দেয়নি। ফিরে এসেছিলাম। একটু পর ভিসি অধ্যাপক ড. ফরহাদ হোসেন আমার বাড়ি এসেছিলেন। উনি খুব লজ্জিত হয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি লজ্জিত হয়েছেন এটাই যথেষ্ট। গেটে যারা ছিল তারা দোষী নয়, দোষী যারা পরিচালনা করে তারা প্রক্টর সাহেব, আপনার পিএস সাহেব। না বলায় যেমন গেট বন্ধ রেখেছে, বলা থাকলে পুরো গেট খুলে রাখত। তাই গেটে পাহারাদারদের কিছু বলা নিজেদেরই অপমান করা। সঙ্গে এও বলেছিলাম, টাঙ্গাইলের মানুষ টাঙ্গাইলের মানুষকে সম্মান করতে জানে না, কোনো দিন করেওনি। হুজুর মওলানা ভাসানী, জননেতা শামসুল হক, জননেতা আবদুল মান্নান, শামসুর রহমান খান শাজাহান, হাতেম আলী তালুকদার, বদিউজ্জামান খান, মির্জা তোফাজ্জল হোসেন, লতিফ সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ এদের কাউকে কোনো দিন সম্মান করেনি। আর কদিনই বা বাঁচব। আমরা মরে গেলে টাঙ্গাইলের লোকজন ঢাকার বড় বড় অফিসে দরজার পিয়নের টুলের সঙ্গে কথা বলবে, ভিতরে যেতে পারবে না। ভিসির পিএস ও প্রক্টর দুজনই টাঙ্গাইলের। সেজন্য অবহেলা তো কিছু থাকবেই। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পাশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। মনে হয় মহাসড়কের দিকেই তিন-চারটা গেট। অন্যদিকে আরও গেট আছে কি না জানি না। দিনে সব গেট খোলা থাকে। কিন্তু মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি গেটের ছয়টিই বন্ধ, কয়েকটি তো ঝালাই করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মেইন গেট যদিও খোলা থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। সন্তোষে শুধু প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, সেখানে হুজুর মওলানা ভাসানী কলেজ আছে, স্কুল আছে, মসজিদ আছে, হুজুরের দরবার হল আছে, সর্বোপরি আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মহামানব অলি-এ-কামেল মওলানা ভাসানীর মাজার আছে। ভক্তরা রাতদিন মাজারে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। সেসব রাস্তাও নাকি বন্ধ করা হয়েছে। এবার ১০ মহররম আশুরার দিনে কোনো মুরিদ মওলানা ভাসানীর কবর জিয়ারতে যেতে পারেনি। আশপাশে একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে। কখন যে দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে আল্লাহ রব্বুল আলামিনই জানেন।
গতকাল ধানমন্ডি ৩২-এর বাড়িতে গিয়েছিলাম। যে সিঁড়িতে পিতার দেহ পড়ে ছিল সেখানে জোহরের নামাজ আদায় করেছি। নামাজ পড়তে গিয়ে চোখে পানি আসা ভালো না। তবু এসেছিল। থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। খুব ভালো লেগেছে যারা ৩২-এর বাড়ি দেখাশোনা করছে তাদের। নামাজ পড়তে গিয়ে একটা চেয়ার চেয়েছিলাম। বড় যত্ন করে চেয়ার এনে দিয়েছিল। মনে হয় ধানমন্ডির ৩২-এর কিউরেটর মো. নজরুল ইসলাম খান পাশে কোথাও বসেন। খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার খুবই ভালো লেগেছে। পুরান যারা ছিল তারা সম্মান করার চেষ্টা করেছে, নতুনরাও করেছে। সহধর্মিণী নাসরীনের শরীরটা বেশ খারাপ। ছেলে দীপ অসুস্থ, মেয়ে কুঁড়ির পরীক্ষা। তাই কুশির সঙ্গে কুশির মাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। বুকের মধ্যে যেমন তোলপাড় করেছে তেমন এক অনাবিল প্রশান্তিও পেয়েছি। পরম প্রভু দয়ালু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার-পরিজন সবাইকে ছায়াতলে রাখেন এবং তাঁদের বেহেশতবাসী করেন। আমার স্ত্রী নাসরীনকেও যেন হেফাজত করেন।
লেখক : রাজনীতিক
www.ksjleague.com সূএ:বাংলাদেশ প্রতিদিন